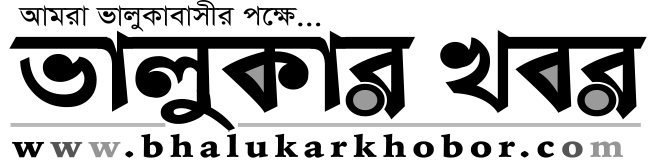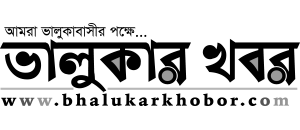পানি, নদী ও বঙ্গবন্ধু
প্রকাশিতঃ ১১:০৫ পূর্বাহ্ণ | আগস্ট ৩০, ২০২১

মো. কামরুল আহসান তালুকদার পিএএ
একজন আপাদমস্তক রাজনীতিক ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তায় উপমহাদেশের সবচেয়ে অগ্রসর বাঙালি জাতিকে তিনি তাই প্রথমবারের মতো স্বতন্ত্র রাষ্ট্র উপহার দিতে পেরেছিলেন। বর্তমান বিশ্ব তাই তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে অভিহিত করে। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেও তিনি কালে কালে হয়ে উঠেছিলেন আপামর বাঙালির ‘বঙ্গবন্ধু’ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা। ইতিহাস, রাষ্ট্র এবং রাজনীতির বাইরেও পদ্মা-যমুনা-মেঘনাবিধৌত এই ভূখণ্ডের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ সম্পর্কেও তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা বিস্ময়কর।
বঙ্গবন্ধুর শৈশবে নদীর ভূমিকার কথা লিখেছেন তাঁর কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তাঁর ‘শেখ মুজিব আমার পিতা’ বইয়ে লেখেন—‘আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠোপথের ধুলোবালি মেখে, বর্ষার কাঁদাপানিতে ভিজে।’
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু প্রায়ই নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন ‘পানির দেশের মানুষ’ হিসেবে। চল্লিশের দশকে রাজস্থানের মরু অঞ্চলে হ্রদ দেখে তাঁর নিজের দেশের কথা মনে হয়েছে। তিনি ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে লিখছেন—‘পানির দেশের মানুষ আমরা। পানিকে বড় ভালোবাসি।’
‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে তিনি লিখেছেন—‘পরের দিন নৌকায় আমরা রওয়ানা করলাম আশুগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন ধরতে। পথে পথে গান চলল। নদীতে বসে আব্বাসউদ্দীন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটি দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতে ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলোও যেন তাঁর গান শুনছে। বঙ্গবন্ধু নৌকা খুব ভালো চালাতে পারতেন। আমার দেখা নয়াচীনে এ বিষয়ে ভালো ধারণা পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন—‘আমার নৌকায় সামনের যে দাঁড় ছিল, প্রথমে আমি দাঁড়টা টানতে শুরু করলাম। কার নৌকা আগে যায় দেখা যাবে! কেউই পারে না, কারণ আমি পাকা মাঝি, বড় বড় নৌকার হাল আমি ধরতে পারি। দাঁড় টানতে, লগি মারতে সবই পারি। পরে আবার হাল ধরলাম। পাকা হালিয়া—যারা আমাদের নৌকার মাঝি তারা তো দেখে অবাক!’ বঙ্গবন্ধু খুব ভালো সাঁতার জানতেন। আমার দেখা নয়াচীনে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছেন—‘আমাদের নৌকার কাছে এসে বলল, আপনারা আমাদের নৌকায় কয়েকজন আসুন। কেউই যেতে চায় না বলে আমি ওদের নৌকায় উঠে পড়লাম। অনেকেই গেল না, কারণ সাঁতার জানে না, ভয়ে এমনিতেই জড়সড়। আমার তো সাঁতার কিছুটা জানা আছে। দু-এক মাইল আস্তে আস্তে সাঁতরাইয়া যাওয়ার অভ্যাসও ছোটকালে ছিল।’
দৈনিক আজাদ পত্রিকার ২০ মে ১৯৫৬ সালের সংখ্যায় আমরা দেখতে পাই, আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যটা এমন ছিল—‘বন্যা পূর্ব্ব পাকিস্তানিদের জীবনে নূতন নয়। কিন্তু বিজ্ঞান সমৃদ্ধ ও সম্পদ বলিষ্ঠ মানুষ অসহায়ের মতো আজও প্রকৃতির রুদ্র পীড়ন সহ্য করিবে কিনা ইহাই হইল সবচেয়ে বড় সওয়াল। হোয়াংহো নদীর প্লাবন, ট্যানিসিভ্যালির তাণ্ডব ও দানিয়ুবের দুর্দমতাকে বশে আনিয়া যদি মানুষ জীবনের সুখ সমৃদ্ধির পথ রচনা করিতে পারে, তবে পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার মতো শান্ত নদীকে আয়ত্ত করিয়া আমরা কেন বন্যার অভিশাপ হইতে মুক্ত হইব না?’
আওয়ামী লীগপ্রধান হিসেবে সত্তরের নির্বাচনের প্রাক্কালে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ‘পানিসম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। বন্যা নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে একটা সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টিকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই। অভ্যন্তরীণ নৌ ও সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ১৯৭০ সালের অক্টোবরের ওই ভাষণের পরপরই নভেম্বরের ১২ তারিখ দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস উপকূলে আঘাত হানে। এতে কমবেশি পাঁচ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। ২৬ নভেম্বর ঢাকার তৎকালীন হোটেল শাহবাগে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) বঙ্গবন্ধু ওই দুর্বিপাক নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি স্পষ্টত বলেন, ‘আজাদীর (ব্রিটিশ থেকে স্বাধীনতার) ২৫ বছর পরেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এমনকি পরিকল্পনা পর্যন্ত তৈরি হয়নি। ঘূর্ণিবার্তা প্রতিরোধ আশ্রয়স্থল নির্মাণের জন্য গত ১০ বছরে মাত্র ২০ কোটি টাকার সংস্থান হয়নি। অথচ ইসলামাবাদের বিলাস-বৈভবের জন্য ২২০ কোটি টাকার অভাব হয়নি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বেই পশ্চিম পাকিস্তানে বাঁধ নির্মাণের জন্য ১০০ কোটি ডলার বরাদ্দের ব্যাপারে কোনো অসুবিধা দেখা দেয়নি। দেশবাসীকে আরেকটি ঘূর্ণিবার্তা ও গোরকীর (জলোচ্ছ্বাস) অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে এক ব্যাপক পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য ব্যাপকভাবে উপকূলীয় বাঁধ ও ঘূর্ণিপ্রতিরোধী পর্যাপ্ত আশ্রয়স্থল নির্মাণ, সুষ্ঠু বিপত্সংকেত ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে।’
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি নদীকে প্রতিরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়ে বলছেন, ‘আমরা ওদের পানিতে মারবো।’ স্বাধীন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বঙ্গবন্ধু নদীর মাধ্যমেই তাঁর ভালো লাগা প্রকাশ করছেন। ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে রেসকোর্স ময়দানের অসম্পাদিত ভাষণটিতে দেখা যায়, তিনি কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উদ্ধৃত করে বলছেন, ‘নম নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি/গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।’
যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে নদী ও বন্দরের প্রয়োজনীয়তা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের ২ তারিখে ঠাকুরগাঁওয়ে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘আমার যে পোর্টগুলো আছে চট্টগ্রাম, চালনা পোর্ট। জাহাজ আসতে পারে না ভালোভাবে। জাহাজগুলো ডুবাইয়া দিয়ে গেছে নদীর মুখে, যাতে জাহাজ আসতে না পারে।’ সদ্যঃস্বাধীন দেশে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু চাঁদপুরে এক জনসভায় বলেছেন, ‘২৫ বৎসর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় তারা করে নাই। নদী-খাল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। না হলেও এক হাজার ৫০০ মাইল নদীপথ নষ্ট হয়েছে। জানি মেঘনায় ভাঙে, মাঝে মাঝে কিছু দিই, জোগাড় করে কিছু কিছু দেওয়া হয়।’ ১৯৭৩ সালের এক জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে নদীভাঙন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দুশ্চিন্তা দেখা যায় কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে—‘নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে কষ্ট হয়। নদী ভাঙছে কত, তোমার জানা আছে যে বাংলাদেশের মানুষ গান গায়—একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা। আমরা চেষ্টা করতে পারি।’
১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলছেন, ‘পাম্প পেলাম না, এটা পেলাম না—এসব বলে বসে না থেকে জনগণকে মবিলাইজ করুন। যেখানে খাল কাটলে পানি হবে, সেখানে সেচের পানি দিন। সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান।’ ১৯৭৩ সালেই বঙ্গবন্ধু নদীখননে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজবাড়ীর পাংশায় চন্দনা-বারাসিয়া নদীখননের মধ্য দিয়ে এই কাজের উদ্বোধন করেছিলেন। তিনি তখনই রাষ্ট্রের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও কিনেছিলেন অন্ততপক্ষে সাতটি ড্রেজার। সমুদ্র ও নদীবন্দর সংস্কার, নৌযান মেরামত এবং বিদেশ থেকে বার্জ-টাগবোট কেনার ক্ষেত্রে তিনি মোটেও কালক্ষেপণ করেননি। তিনি পাকিস্তানের কারাগার থেকে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরলেন আর ১৯ মার্চে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে নদীর প্রসঙ্গ তুললেন। কী হবে অভিন্ন নদীগুলোর ভবিষ্যৎ! যৌথ নদী কমিশন বা জেআরসি গঠনের আলোচনা হবে এবং ওই বছরের নভেম্বরে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
দেশভাগের ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শী বঙ্গবন্ধু জানতেন ভূ-রাজনীতিতে দক্ষ নেহরু তৎকালীন ভারত ও পাকিস্তানের সীমারেখা এমনভাবে চেয়েছিলেন, যাতে করে তৎকালীন পাকিস্তান পানিসম্পদের ক্ষেত্রে ভারতনির্ভর থাকে। আর পাকিস্তান নেতৃত্ব ভূ-রাজনীতি ভুলে গিয়ে তাৎক্ষণিক ও ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কিভাবে একের পর এক হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই আক্ষেপ আমরা দেখি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে।
পানি ও নদীর একান্ত আত্মীয় বঙ্গবন্ধু পানির মতো স্বচ্ছ হৃদয়ে বাঙালি জাতিকে আমৃত্যু ধারণ করেছেন।
লেখক : পানিসম্পদ উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব)